বাংলাদেশে ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে ৩৪৪ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ
জেম ফাউন্ডেশনের গবেষণা
জাগো বাংলা প্রতিবেদন
প্রকাশ: ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ০৩:৫৬ এএম
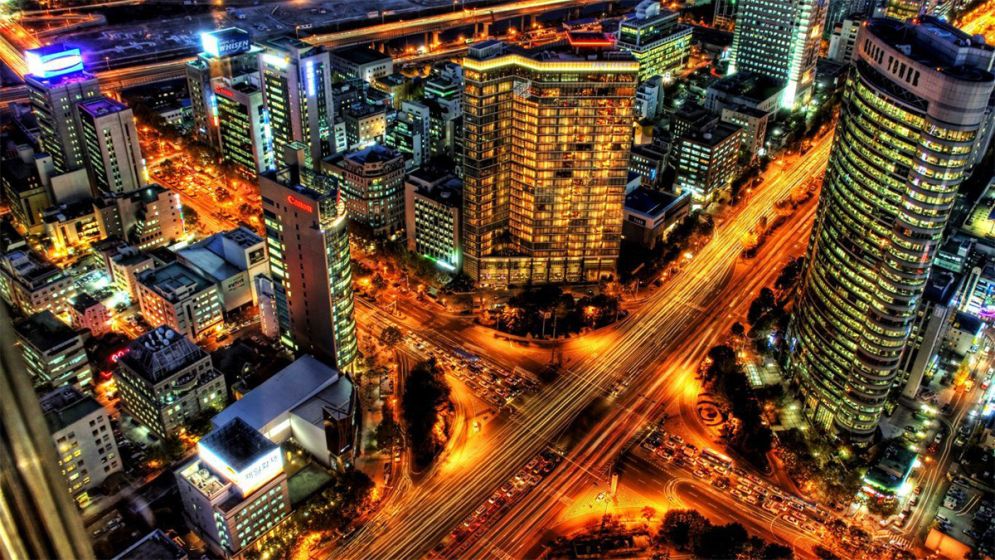
দীর্ঘদিন ধরেই দেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের শঙ্কার কথা বলে আসছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও সে ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি নেই বললেই চলে। শুক্রবার সকালে সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করেছে বাংলাদেশ। ৫ দশমিক ৭ মাত্রার এ ভূমিকম্পকে ‘ভবিষ্যতের বড় ভূমিকম্পের সতর্কবার্তা’ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। গতকালও তিনদফা ভূমিকম্পে কেঁপেছে দেশ।
বড় মাত্রার ভূমিকম্প হলে দেশে ৩৪৪ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ ক্ষতির মুখে পড়তে পারে বলে আন্তর্জাতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে। সারা দেশে ঝুঁকির মুখে থাকা ভবন প্রতিস্থাপনে ব্যয় হতে পারে ৩৫৬ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৭৭ শতাংশ। বিশ্লেষকরা বলছেন, ঝুঁকিতে থাকা ভবন খুঁজে বের করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না নেয়া হলে বড় ধরনের মানবিক ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে বাংলাদেশ।
জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সহায়তায় ২০২৩ সালে ‘ভূমিকম্পে দুর্বলতা এবং বাংলাদেশে পদ্ধতিগত ঝুঁকি মূল্যায়ন’ শীর্ষক একটি অন্তর্বর্তীকালীন গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে ইতালির গ্লোবাল আর্থকোয়াক মডেলিং (জেম) ফাউন্ডেশন।
প্রতিবেদনে বাংলাদেশ এবং তার চারপাশের সক্রিয় ফল্ট জোন থেকে উদ্ভূত ভূমিকম্পের ঝুঁকির মুখে দেশে বিরাজমান বড় ধরনের দুর্বলতার বিষয়টি উঠে এসেছে। এ প্রতিবেদনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি বিস্তারিত, উন্মুক্ত ভূমিকম্প ঝুঁকি মডেল তৈরি এবং বর্তমান ঝুঁকি মূল্যায়ন করা। এতে দেশের বেশির ভাগ ভবনের নকশা ও নির্মাণকৌশল ভূমিকম্প প্রতিরোধী না হওয়া, অপ্রকৌশলগত কাঠামোর ব্যাপকতা, বিল্ডিং কোড না মানা এবং নদীর বদ্বীপে সহজে তরলীকরণযোগ্য মাটির উপস্থিতি ঝুঁকিকে মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
জেম ফাউন্ডেশনের গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ভূমিকম্প ঝুঁকি মূল্যায়নে গ্লোবাল আর্থকোয়াক মডেলের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্পদের ঝুঁকি, ভূমিকম্পের বিপদ ও দুর্বলতার দিকগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সম্পদের ঝুঁকির ক্ষেত্রে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প সম্পদের ভৌগোলিক অবস্থান ও মূল্য বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে দেশের সাতটি অঞ্চলের সম্পদের (ভবন) সংখ্যা ধরা হয়েছে ২ কোটি ৯০ লাখ। ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকা এ সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ৩৪৪ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির ৭৪ শতাংশ।
ভূমিকম্পের ক্ষতি থেকে এ সম্পদ রক্ষা করতে প্রতিস্থাপন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫৬ বিলিয়ন বা ৩৫ হাজার ৬০০ কোটি ডলার। ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সম্পদের পরিমাণ ও প্রতিস্থাপন ব্যয় হবে সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে ঢাকার ৯০ লাখ ভবন প্রতিস্থাপনে ১৪৯ বিলিয়ন ডলার বা ১৪ হাজার ৯০০ কোটি ডলার এবং চট্টগ্রামে ৫০ লাখ ভবন প্রতিস্থাপনে ব্যয় হবে ৬২ বিলিয়ন ডলার বা ৬ হাজার ২০০ কোটি ডলার। রাজশাহীতে ৪০ লাখ ভবনের প্রতিস্থাপনে ৪২ বিলিয়ন ডলার ও খুলনার ৩০ লাখ ভবন প্রতিস্থাপনে ব্যয় হবে ৩৪ বিলিয়ন ডলার। রংপুরের ৪০ লাখ ভবনের ক্ষেত্রে খরচ হবে ৩৪ বিলিয়ন ডলার। বরিশাল ও সিলেটের ২০ লাখ করে ভবন প্রতিস্থাপনে ব্যয় হবে ১৭ বিলিয়ন ডলার করে। দেশজুড়ে ভবনগুলো কী ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি সেটিও উঠে এসেছে আলোচ্য প্রতিবেদনে। এক্ষেত্রে সংখ্যায় পিছিয়ে থাকলেও কংক্রিটের ভবনগুলো প্রতিস্থাপনে সবচেয়ে বেশি, ২৮ শতাংশ অর্থ ব্যয় হবে।
বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কী তীব্রতায় এবং কত ঘন ঘন ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি হতে পারে সেটি বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে বিপদের মাত্রা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সিসমিক বিপদের মাত্রা দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে সক্রিয় ফল্ট লাইনের কাছাকাছি কেন্দ্রীভূত।
জেম ফাউন্ডেশনের গবেষণা মতে, ঢাকা অঞ্চলে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের মূল্য ৬৯ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার থেকে ১৬৭ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের মূল্য ৪৭ দশমিক ৮ বিলিয়ন থেকে ৬৯ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার। রাজশাহীতে ৩৯ দশমিক ১ বিলিয়ন থেকে ৪৭ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার। রংপুর ও খুলনা অঞ্চলে ১৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন থেকে ৩৯ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার। সিলেট ও বরিশাল অঞ্চলের সম্পদের মূল্য ১৮ দশমিক ৯ বিলিয়ন থেকে ১৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার।
গবেষণা প্রতিবেদনটি তৈরিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ ও ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগ, বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগ, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ, ইউএনডিপি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কারিগরি প্যানেল গঠন করা হয়েছিল। এ কারিগরি প্যানেলের অন্যতম দুই সদস্য ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ হুমায়ূন আখতার ও বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী।
গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফলকে যথাযথ বলে মন্তব্য করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ এবং আরএম ও পিআর ইউনিট) কেএম আবদুল ওয়াদুদ। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে কোনো পূর্বাভাস নেই। তাই এক্ষেত্রে প্রস্তুতিটাই বড় বিষয়। মূল কাজ হলো বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ।
রানা প্লাজা ধসের পর ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট এলাকার বিল্ডিংগুলো ঝুঁকি অনুযায়ী কালার কোড করার প্রস্তাব করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা ভবনগুলো চিহ্নিত করেছেন এবং যেগুলো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলো লাল রঙ, যেগুলো কম ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলো হলুদ রঙ এবং যেগুলো বিল্ডিং কোড মেনে বানানো হয়েছে সেগুলো সবুজ রঙ করার সুপারিশ করেছেন। পরবর্তী সময়ে সে তালিকাটি আর প্রকাশ করা হয়নি। আমি মনে করি, এ তালিকা এখন প্রকাশ করা প্রয়োজন। এতে মানুষের সচেতনতা বাড়বে। ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো রেট্রোফিটিং করে মেরামত করতেই হবে। পাশাপাশি রাজউকের রেগুলেটরি কাজে যেন কোনো ছাড় দেয়া না হয়। আমরা এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার জন্য রাজউককে বলব।’
ভূমিকম্পে আর্থিক ক্ষতি কমিয়ে আনতে দুর্বল ভবনে রেট্রোফিটিং প্রযুক্তির কথা বলছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। সাভারে রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর দেশব্যাপী বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে পরিচালিত হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন ভবন চিহ্নিত করার কাজ। এসব ভবন না ভেঙে সহজ সমাধানের নাম হলো রেট্রোফিটিং। যথাযথভাবে যদি কাজটি করা যায়, তাহলে ভবনের স্থায়িত্বও বেড়ে যায় ৫০ বছর বা তারও বেশি।
এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসারী বলেন, ‘আমরা একটি মডেলিংয়ের মাধ্যমে দেশের সাতটি অঞ্চলের ভবনগুলো নিয়ে একটা পূর্বাভাস দিয়েছিলাম। তবে সঠিক চিত্র পেতে হলে প্রতিটি ভবনের নমুনা আলাদাভাবে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা দরকার। বিশেষ করে ঢাকায় অতিসত্বর এ ধরনের ভবনগুলোর চেকিং দরকার। এজন্য সরকারের কোনো অর্থ ব্যয় হবে না। রাজউক একটা ঘোষণা দেবে, যাদের ভবনে ত্রুটি আছে তারা রেট্রোফিটিং করে সার্টিফিকেট জমা দিয়ে যাবে। নয়তো ওই ভবনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হবে। তাহলেই কিন্তু সবাই এটা করতে বাধ্য।’
শুক্রবারের ভূমিকম্পে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ভবনে ফাটল ধরার প্রসঙ্গ টেনে এ বিশেষজ্ঞ বলেন, ‘এমন ক্ষয়ক্ষতি হবেই।’ একটি বড় ভবন ধসে পড়লে কতটা ক্ষতি হতে পারে, তা বোঝাতে গিয়ে ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দেন অধ্যাপক আনসারী। সেজন্য সরকারের এখনই বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শুক্রবার রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকা শহরের যত স্থাপনায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, ভবন ডেবে গেছে, ফাটল হয়েছে তার তুলনায় ৭ মাত্রার হলে ক্ষয়ক্ষতি অনেক গুণ বেড়ে যাবে। অনেক ভবন ভেঙে পড়া, বহু মানুষ হতাহত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। ঢাকার ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে এমন ভূমিকম্প হলে দুই-তিন লাখ মানুষ হতাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, ভেঙে পড়তে পারে ঢাকা শহরের ৩৫ শতাংশ ভবন।
